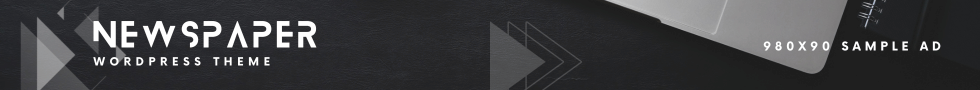মায়ানমারে ধ্বংসস্তূপ। উদ্ধারকাজ চলায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ২,০৫৬ জনেরও বেশী। সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা প্রশাসনের। মায়ানমারে ভূমিকম্পে আহত ৩,৯০০। নিখোঁজ প্রায় ৩০০। এক সপ্তাহ ধরে জাতীয় শোকপালনের বিবৃতি জুন্টা সরকারের। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম অধ্যুষিত দেশের প্রায় ৬০টি মসজিদ। মায়ানমারের প্রায় ৬০টি মসজিদে রমজান মাসের জুম্মার নমাজ চলাকালীন ভূমিকম্পে ৭০০ জন মুসলিমের মৃত্যু বলে দাবি রিপোর্টে। মায়ানমারের ভূমিকম্পে মৃত্যুমিছিল।
মায়ানমারে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ। ভেঙে পড়া অধিকাংশ মসজিদই ১৯ শতকে তৈরি। ভূমিকম্পে ১৫৯১টি বাড়ি, ৬৭০টি বৌদ্ধ মঠ, ৬০টি স্কুল, তিনটি সেতু, ২৯০টি প্যাগোডা ক্ষতিগ্রস্ত এই ভূমিকম্পে। ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বহু সদস্য মায়ানমারে ধ্বংসস্তূর সরানোর কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। এনডিআরএফ কর্মীরা অন্তত ৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পাঁচটি দেহ মিলেছে ইউ হ্লা থিয়েন বৌদ্ধ মঠ থেকে। আশঙ্কা, মন্দালয়ে অবস্থিত এই মঠে ১৭০ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চাপা পড়ে গিয়ে থাকতে পারেন। ভারতের এনডিআরএফ কর্মীরা ১৩টি স্থানে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। মন্দালয়ের একটি ভেঙে পড়া বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে চারজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার। তাঁদের মধ্যে এক ছোট্ট মেয়ে এবং এক গর্ভবতী মহিলাও আছেন।
মায়ানমারের ভূমিকম্পের এতদিন পরে ব্যাঙ্ককে ভেঙে পড়া সেই বহুতলের নীচে কারও বেঁচে থাকার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন থাই কর্তৃপক্ষ। ধ্বংসস্তূপের একটি অংশে নাকি এখনও বেঁচে থাকতে পারেন অনেকে। সেখানে প্রাণের চিহ্ন মিলেছে। ব্যাঙ্ককের ডেপুটি গভর্নর তাভিদা কামোলবেজ জানান, উদ্ধারকারী দলকে ধ্বংসস্তূপের সেই অংশে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে তাভিদা বলেন, ‘আমরা হাল ছাড়ব না’। ভূমিকম্পে ১৫৯১টি বাড়ি, ৬৭০টি বৌদ্ধ মঠ, ৬০টি স্কুল, তিনটি সেতু, ২৯০টি প্যাগোডা ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এনডিআরএফ কর্মীরা ৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। পাঁচটি দেহ মিলেছে ইউ হ্লা থিয়েন বৌদ্ধ মঠ থেকে। আশঙ্কা, মন্দালয়ে অবস্থিত মঠে ১৭০ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চাপা পড়ে গিয়ে থাকতে পারেন। ভারতের এনডিআরএফ কর্মীরা ১৩টি স্থানে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।
প্রসঙ্গত, মায়ানমারে ভূমিকম্প রিখটার স্কেলে ৭.৭। উৎসস্থল ছিল মায়ানমারের মান্দালয় শহরের কাছে। প্রায় ১৫ বার ভূকম্প পরবর্তী কম্পন বা আফটার শক। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মান্দালয়। ভূমিকম্পের জেরে ভেঙে পড়েছে হাজার হাজার বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি, মোবাইলের টাওয়ার। ফাটল ধরেছে সড়ক, সেতুতে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত এলাকায়। ভূমিকম্পের কারণে ঘরছাড়া হাজার হাজার মানুষ। রাজধানী নেপিডোয়ে বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে রাত কাটাচ্ছেন। অনেকে আবার কোলের সন্তানকে নিয়ে রাস্তায় চাদর পেতে শুয়ে রয়েছেন। মান্দালয়েও একই অবস্থা। ভূমিকম্পে মায়ানমারে মৃতদের মধ্যে তিন জন চিনের নাগরিক। ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভূমিকম্পে তাদেরও দু’জন নাগরিক মারা গিয়েছেন। প্রতিবেশী তাইল্যান্ডেও ভূমিকম্পের প্রভাব। রাজধানী ব্যাঙ্ককে একটি নির্মীয়মাণ ৩০ তলা ভবন ভেঙে পড়ে ১৭ জনের মৃত্যু। আহত অবস্থায় উদ্ধার ৪২ জনকে। ৭৮ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ধারকারীদের অনুমান,ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে।
ভূমিকম্পের আশঙ্কা কলকাতাতেও। ভূতাত্ত্বিকদের গবেষনা বলছে, বিভিন্ন ফাটল বা চ্যুতিরেখা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকায় হিমালয়ের গভীর থেকে বা আরাকান-ইয়োমার দিক থেকে আসা প্রায় সব কম্পন কলকাতায় পৌঁছে যায়। কলকাতার মাটির তলায় থাকা ইওসিন হিঞ্জ উচ্চ হিমালয় বা মায়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত না হলেও সরাসরি মেঘালয়ের ‘ডাওকি ফল্টে’ মিশেছে। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে বা শিলং পাহাড়ে পৌঁছনো যে কোনও কম্পন কলকাতাকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম। কলকাতা, রাজারহাট, রানাঘাট, শিলং। তিব্বতে না গেলেও সে রাস্তাও এক শীতল দেশেই গিয়ে মিশে যাচ্ছে ভূস্তরের এক বড়সড় ফাটলের সঙ্গে। কলকাতার দিকে ধেয়ে আসতে পারে মায়ানমারের মতো কোনও বিপদ। ভূতত্ত্ববিদরাও একমত। ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বঙ্গোপসাগর থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ভূমিকম্প। সমুদ্রপৃষ্ঠের ৯১ কিলোমিটার গভীরে ছিল তার উৎসস্থল। কলকাতা থেকে সেই উৎসস্থলের দূরত্ব ছিল ৩৩০ কিলোমিটার। ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ২২০ কিলোমিটার।
মায়ানমার এবং তাইল্যান্ডর মান্দালয়ের নীচে ভূস্তরে ‘সাগাইং ফল্ট’ নামে যে সুদীর্ঘ ফাটল বা ‘চ্যুতিরেখা’ থেকেই কম্পন। ভূস্তরের এই সব ফাটল বা দুর্বল অংশই সাধারণত ভূমিকম্পের জন্ম দেয়। কলকাতা শহর উদ্বেগের কারণ বলে মনে করছেন ভূতত্ত্ববিদরা। কারণ, কলকাতার অবস্থানও এই রকমই এক ভূতাত্ত্বিক রেখার ঠিক উপরেই। সে রেখা কোনও ফাটল নয়। মহাদেশীয় পাতের ভাঙনের রেখা। যার গভীরে ফাটল থাকতে পারে বলে ভূতাত্ত্বিকদের অনুমান। ফাটল না থাকলেও ওই অঞ্চল থেকে ভূমিকম্পের আশঙ্কা প্রকাশ ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে। ভারতীয় পাত বা ইন্ডিয়ান প্লেট, কুমেরু পাত বা অ্যান্টার্কটিক প্লেট এবং অস্ট্রেলীয় পাত বা অস্ট্রেলিয়ান প্লেট ১৩ কোটি বছর আগে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। যে রেখা বরাবর তারা পরস্পরের থেকে এখন বিচ্ছিন্ন, সেখানেই ইওসিন হিঞ্জের অবস্থান। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলের ভূস্তরের সঙ্গে ভারতের পূর্ব উপকূলের ভূস্তর মিলে যায়। দাক্ষিণাত্য থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একই প্রবণতা। ওড়িশার উত্তরে উপকূলরেখা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, মায়ানমার অস্ট্রেলীয় পাতের ভূস্তরের মিল রয়েছে বলে ভূতাত্ত্বিকদের দাবি। অর্থাৎ, বর্তমান অস্ট্রেলীয় পাত এবং কুমেরু পাত ‘অতিমহাদেশীয় সুপারকন্টেনেট যুগে’ ভারতীয় পাতের সঙ্গেই জুড়ে ছিল। ‘অতিমহাদেশীয় পাতে’ যে রেখা বরাবর ভাঙন ধরেছিল, আজকের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে সেই অঞ্চলই ‘ইওসিন হিঞ্জ’ অঞ্চল নামে চিহ্নিত। বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর উঠে এসে এই রেখা কলকাতার তলা দিয়ে রাজারহাট এবং রানাঘাট হয়ে বাংলাদেশের দিকে বাঁক নিয়েছে। পরে আবার কিছুটা উত্তরে বাঁক নিয়ে তা ভারতের মেঘালয়ে ঢুকে শিলং পাহাড়ের দক্ষিণে গিয়ে শেষ। শিলং পাহাড়ের দক্ষিণেই রয়েছে ভূস্তরের ‘ডাওকি ফল্ট’ নামে বিপজ্জনক ফাটল। সেখানে গিয়েই মিশেছে এই ইওসিন হিঞ্জ। কলকাতার অবস্থান সেই হিঞ্জের উপরেই।
ভূতত্ত্ববিদের কথায়, মানচিত্রে যেখানে দক্ষিণবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অংশে এক সময়ে স্থলভাগই ছিল না। সুপার কন্টিনেন্ট বা অতিমহাদেশীয় পাতে ভাঙন ধরার পরে ওই অঞ্চল জলের তলায় ছিল। পলি জমতে জমতে পরে স্থলভাগে পরিণত হয়। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে ভারতের পূর্ব তটরেখা বরাবর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের আগে পর্যন্ত যে অংশ, সেখানে শেল্ফ বা ধাপের মতো ভূস্তর রয়েছে। অর্থাৎ, মহাদেশীয় পাত যেখান থেকে ভেঙেছিল, সেখানে ভাঙনের চিহ্ন স্পষ্ট। ভাঙনের রেখা বরাবর ভূস্তরের গঠন ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। ওড়িশার উত্তর দিক পর্যন্ত সেই ধাপ দৃশ্যমান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে এসে সেই ধাপ বা শেল্ফ জাতীয় ভূস্তরের দেখা পুরোটা মেলে না। কারণ, পলি জমে স্থলভাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া। দীর্ঘ দিন ধরে পলি জমতে জমতে শেল্ফ বা ধাপের মতো অংশ পলির পুরু স্তরের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। সেই স্তরই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা তৈরি করেছে। যে এলাকায় এখন দক্ষিণবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবস্থান। ইওসিন হিঞ্জের পশ্চিম এবং উত্তর দিকে যে অঞ্চল, সেই এলাকা ভাঙনের পরেও স্থলভাগেই ছিল। হিঞ্জের পূর্ব এবং দক্ষিণে স্থলভাগ ভাঙনের পরে সেই অঞ্চল জলভাগে চলে গিয়েছিল। পলি জমতে জমতে ফের তা স্থলভাগ হয়ে উঠেছে। কলকাতা অবস্থান ঠিক ভাঙনের রেখার উপরেই। ওই রেখার নীচে, অর্থাৎ ইওসিন হিঞ্জের নীচে ভূস্তরে ফাটল থাকার সম্ভাবনা। ইওসিন হিঞ্জ অঞ্চলের নীচে ফাটল। ইওসিন হিঞ্জ অঞ্চল নিজেই ভূস্তরের একটা দুর্বল জায়গা। এই অঞ্চল আগেও ভূকম্পনের জন্ম দিয়েছে। ইওসিন হিঞ্জ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের গভীরে ৮৫ ডিগ্রি ইস্ট রিজ নামের একটি রেখায় কিছু ফাটল বা দুর্বল অংশ কিছু বছরে সক্রিয় হতে পারে। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বঙ্গোপসাগরের ওই অঞ্চল থেকে জন্ম নেওয়া ভূমিকম্পের কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠের ৯১ কিলোমিটার গভীরে ছিল তার উৎসস্থল। কলকাতা থেকে উৎসস্থলের দূরত্ব ছিল ৩৩০ কিলোমিটার। আর ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ২২০ কিলোমিটার। ফলে পায়ের তলায় থাকা ইওসিন হিঞ্জ আর কয়েকশো কিলোমিটার দক্ষিণে থাকা ৮৫ ডিগ্রি ইস্টরিজ কলকাতার জন্য দুই অঞ্চলই সমান উদ্বেগের। এই অঞ্চল থেকে তৈরি কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬ অতিক্রম করবে না।
রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার বেশি কম্পন আসতে পারে ভারতের উত্তর সীমান্ত এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ও পার থেকে। কারণ, ভারতীয় পাত ক্রমশ উত্তর দিকে অর্থাৎ ইউরেশীয় পাতের দিকে সরছে। দুই পাতের সংযোগস্থলে যে চ্যুতিরেখা, তা ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতি অংশ ইয়ারলুং সাংপো বরাবর অবস্থান। ওই অঞ্চলে জন্ম নেওয়া কোনও ভূমিকম্প কলকাতায় বড় ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে বলে ভূবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ও পারে অর্থাৎ মায়ানমারের মাটির তলায় একাধিক ফাটল তথা চ্যুতিরেখা সক্রিয়। ভারতীয় পাত, ইউরেশীয় পাত, বর্মী পাত, সুন্ডা পাত পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে মায়ানমারের নানা অংশে। আরাকান ইয়োমা সুমাত্রা পর্বত শ্রেণি অঞ্চল সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখানকার যে কোনও কম্পন উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বড় ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা। কলকাতার ভূস্তর শক্ত পাথুরে হলে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা ধাক্কা অনেকটা প্রশমিত করে নিতে পারত। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী গোটা সমভূমি অঞ্চল নরম পলির স্তরে গঠিত। তাই কম কম্পনেও বেশি ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা।